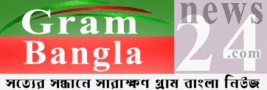টাইম ম্যাগাজিন আজই তাদের অনলাইনে রোহিঙ্গারা এই সম্মেলনে বাদ পড়ায় উষ্মা প্রকাশ করেছে। কারণ, রোহিঙ্গাদের বাদ দিয়ে এই শান্তি সম্মেলন নৈতিকভাবে একটি প্রশ্নবিদ্ধ সম্মেলন থেকে যাবে। টাইম রিপোর্ট স্মরণ করেছে যে সু চির এনএলডিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তারা যেন ‘রোহিঙ্গা’ শব্দটি উচ্চারণ না করেন। এর পরিবর্তে এনএলডি প্রশাসন তাদের ‘রাখাইনের মুসলিম’ হিসেবে আখ্যা দিচ্ছে। আশা করব, এই অঞ্চলে সু চি এমন কিছু করবেন না, যা তাঁকে জেনারেল ইয়াহিয়াদের দলে নিয়ে যেতে পারে। পাকিস্তানি জেনারেলরা ‘বাঙালি’ বুঝতে চাননি। বাঙালি দমানো সম্ভব হয়েছিল; কিন্তু তা মাত্র ২৩ বছরের জন্য! মিয়ানমারের ১০ লাখের বেশি মুসলিম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী নাগরিকত্ব, ভোটাধিকার এবং চাকরির অধিকারের দাবিতে সংগ্রামরত।
মঙ্গলবারের সংবাদ সম্মেলনে বান কি মুন যথার্থই বলেন, ‘রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের বিষয়টি কেবল তাঁদের আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন নয়। এই মানুষগুলো অনেক প্রজন্ম ধরে এ দেশে বাস করছেন। দেশের অন্য নাগরিকেরা নাগরিকত্ব বা যে আইনি স্বীকৃতি পান, তাঁদেরও তা পাওয়ার অধিকার আছে।’ বিশ্বে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে কখনো কখনো বড় পার্থক্য দেখানো হয়। আমাদের মনে হয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দুটি বিষয়ে খুব বড়মাপের চাপ দিতে হবে। প্রথমত, রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দেওয়া। কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি, এ বিষয়ে সু চির নতুন সরকার সহজে নড়াচড়া করবে না। অং সান সু চির রোহিঙ্গাবিরোধী মনোভাব ইতিমধ্যে স্পষ্ট হতে বাকি নেই। তদুপরি আশা করতে পারি, তিনি এ বিষয়ে নির্মূল কর্মসূচিতে না গিয়ে নীরবতা পালনে ব্রতী হতে পারেন। এটা হয়তো নেহাত কাকতালীয় নয় যে বান কি মুন সু চির উপস্থিতিতে কথাটা তুলেছেন এবং সু চি অন্তত তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন বলে আমরা জানতে পারিনি। সুতরাং এটা সামান্য হলেও অগ্রগতি।
মিয়ানমারের উন্নয়ন অংশীদারদের বান কি মুনের সুরে তাল মেলাতে হবে। মিয়ানমারের মানবাধিকারের রেকর্ড প্রশ্নে রোহিঙ্গা প্রশ্নকে একটা বড় কলঙ্ক হিসেবেই দেখিয়ে যেতে হবে। কারণ, মানবসভ্যতার এই প্রান্তে পৌঁছে জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র থেকে এত বড় একটা সভ্যতাবিরোধী কাজ মিয়ানমারকে করতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু সে জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির দরকার আছে। মিয়ানমারের সামরিক ও বেসামরিক নেতারা, সুশীল সমাজকে বিষয়টি আরও ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে দিতে হবে। সে জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় যে দিকটি আমি বলব, সেটি নিশ্চিত করতে কোনো অপেক্ষার প্রহর গণনা করা চলবে না।
২০১২ সালে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ১ লাখ ২০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের অনেকেরই ঠিকানা এখন কমবেশি দুর্দশাগ্রস্ত আশ্রয়শিবির। হাজার হাজার রোহিঙ্গা উন্নত জীবন কিংবা স্রেফ প্রাণে বাঁচার আশায় উত্তাল ঊর্মিমালা পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ‘আশ্রয়’ নিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই সাগরপথে ডুবে মরে হাঙর-কুমিরের খাদ্যে পরিণত হয়েছেন। কিংবা মানব পাচারকারীদের খপ্পরে পড়েছেন। দশকের পর দশক কাটিয়ে, বিশেষ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর যেখানে দেশটির স্বাধীনতাসংগ্রামে ভূমিকা রয়েছে; যেখানে তাঁরা বহু বছর ধরে জাতীয় পার্লামেন্টে আসনও লাভ করেছেন, সেখানে আকস্মিকভাবে তাঁদের ‘রাষ্ট্রবিহীন’ করার প্রচেষ্টা অবশ্যই নিন্দনীয় ও অমার্জনীয়।
জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন শান্তি সম্মেলনকে ‘ঐতিহাসিক’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ এ দেশে অনেক প্রাণহানি ঘটিয়েছে। কয়েক প্রজন্ম এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুন বলেন, ‘এটি এখন স্পষ্ট যে আপনাদের মতভিন্নতার কোনো সামরিক সমাধান নেই।’ আমরা এর সঙ্গে যেটি যোগ করব, সেটি হলো, এটা প্রতীয়মান হওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হবে যে দেশটি তার সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সংলাপ করবে আর তাদের রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে সামরিক সমাধান খুঁজবে। রোহিঙ্গা সমস্যারও কোনো সামরিক সমাধান নেই। এর একটা রাজনৈতিক সমাধান হতে হবে।
সম্মেলনে যোগদানকারী ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে নোবেলজয়ী সু চি বলেন, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয় সাধন বা জাতীয় ঐক্য গড়তে না পারছি, ততক্ষণ আমরা একটি শান্তিপূর্ণ দেশ গড়তে পারব না। আমরা একতাবদ্ধ হলেই কেবল শান্তি আসবে। আর শান্তি ফিরে এলেই আমরা এ অঞ্চলের অন্য দেশ এবং বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারব।’ সু চিকে দ্রুত বিবেচনায় নিতে হবে, রোহিঙ্গা প্রশ্নে যে নীতি তাঁরা নিয়েছেন, তা জিইয়ে রেখে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতি আশা করা যাবে না। ওই শান্তি সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফেদেরিকা মগেরিনি। যুক্তরাষ্ট্রও মনে করে, ‘শান্তি আনতে এটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ’।
আমরা আশা করব, ইউরোপ, আমেরিকা জোরেশোরে রোহিঙ্গা ইস্যুতে মুখ খুলবে। তারা মুখ খুলেছে; কিন্তু তা কার্যকর অর্থে হতে হবে। মিয়ানমারের নতুন সরকারকে এটা পরিষ্কার করে বলতে হবে, নাগরিকত্ব প্রদানের প্রক্রিয়া তারা ধীরে ধীরে সুরাহা করার নীতি অনুসরণ করলেও মানবাধিকার যেকোনো মূল্যে সমুন্নত রাখতে হবে। কিছু মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে কিছু বৈষম্য দূর করা তাদের পক্ষে এখনই সম্ভব না হতে পারে। কিন্তু জাতিগত পরিচয়ের কথা তুলে রোহিঙ্গাদের ওপর রাষ্ট্রীয় বাহিনীর দমনপীড়ন-নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।
শুধু রোহিঙ্গা বলে নয়, জাতিসংঘের কোনো সদস্যরাষ্ট্রই বিচারবহির্ভূত কোনো উপায়ে কোনো গোষ্ঠীকে নির্মূল করতে পারে না। সু চির রয়েছে দীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাস। তিনি আটপৌরে নির্বাচিত জননেত্রী নন। নোবেলজয়ী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব আছে রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতার ওপরে বিবেক ও ন্যায়বিচারের নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে জিরো টলারেন্স নীতি প্রত্যাশিত। কেউ যাতে বলতে না পারে তারা দ্বৈতনীতি অনুসরণ করছে। বর্ণবাদী ও ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে বিশ্বজুড়ে একটা উন্মাদনা চলছে। যে বিশ্ব উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে লড়ছে, সেই বিশ্বকে যেকোনো দেশে, যেকোনো স্থানে এবং তার নামকরণ যা-ই হোক না কেন, উগ্রবাদ ও জঙ্গিত্বকে প্রশ্রয় নয়, তার সর্বাত্মক বিরোধিতা করতে হবে। দুঃখজনক যে রোহিঙ্গারা পদ্ধতিগতভাবে রাষ্ট্রীয় উগ্রপন্থা বা জঙ্গিপনার শিকার হচ্ছেন।
এটা আশাব্যঞ্জক, সু চি রাখাইন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিশন করেছেন। আমরা এই প্রতিবেদনের দিকে তাকিয়ে থাকব, যদিও এই কমিশনে রোহিঙ্গাদের কোনো প্রতিনিধি রাখা হয়নি।

কোন সু চি রোহিঙ্গাবিরোধী? জননেত্রী নাকি নোবেলজয়ী?
দুটি বিষয় চোখে পড়ল। প্রথমত, বান কি মুন গত মঙ্গলবার দেশটির অঘোষিত প্রধান অং সান সু চির উপস্থিতিতেই সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানালেন। দ্বিতীয়ত, মিয়ানমারের জাতিগত সংখ্যালঘু সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে এর পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে জাতিসংঘের মহাসচিবের উপস্থিতিতেই শান্তি আলোচনা শুরু করেছে দেশটির নতুন নির্বাচিত সরকার। আশা করা হচ্ছে, এই আলোচনা সফল হলে দেশটিতে কয়েক দশক ধরে চলা সংঘাতের অবসান হবে। এর নাম হলো প্যাংলং সম্মেলন। ১৭টি সশস্ত্র গোষ্ঠীর প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু এই আলোচনায় রোহিঙ্গারা নেই। যদিও কখনো কখনো সশস্ত্র রোহিঙ্গা গোষ্ঠীর তৎপরতার উদ্বেগজনক খবর আমাদের কানে এসেছে।